প্রশান্ত ভট্টাচার্য, সিনিয়ার জার্নালিস্ট, কলকাতা:
জানি না শরৎ কাল আসে বলে কাশফুলে মাঠ ঢাকে নাকি, কাশফুল এসেছে বলে শরতের আগমন হয়েছে। আর তাই আগমনি। কাশফুল আর শিউলি ফুলের সুবাসের প্রাকৃতিক ব্লেন্ডিং জানান দিচ্ছে দুর্গাপুজো এসে গেছে। বাঙালি হিন্দুদের সর্বাত্মক মাতানো উৎসব দুর্গাপুজো আর দূরে নেই। মহালয়া। তার মানে বরকে কৈলাসে রেখে দুই মেয়ে ও দুই ছেলেকে নিয়ে উমা রওনা দিয়ে দিলেন। সঙ্গে সব পোষ্যগুলো। কেননা, নেশাখোর স্বামী ওই প্রাণীগুলোকে টাইম টু টাইম খাওয়ার দেবে কি না, তার ঠিক আছে! তার চে' বরং আমার সঙ্গে থাকলে পর
মা মেনকার কাছে দু'বেলা ভালমন্দ খাবারটা পাবে। আর ছেলেমেয়ে কটাকে একটু চোখে চোখে রাখতে পারবে। বাড়ির বাগালটাকে বলেছিলুম, এবার থেকে যা, কত্তাকে একটু নজর রাখতে পারবি। বলে কিনা, না মা, তোমার সঙ্গেই যাব৷ বাবুর কোনো ঠিক নেই। তাছাড়া, আমারও তো একটু বেড়ানো হয়। চারদিন কোনো কাজ নেই, শুধু তোমার চরণতলে পোজ দেওয়া ছাড়া। এই এক শারদা দুর্গা যখন শিবের কাছে গিয়েছে রওনা হওয়ার শুভক্ষণটি জেনে নিতে, তখন দেবাদিদেব বললেন, যিনি নিজে সর্বমঙ্গলা তাঁর সবক্ষণই শুভক্ষণ, সব মুহূর্তই পুণ্যমুহূর্ত। ওদিকে তখনই ওলা না উবার, কীসে করে মামাবাড়ি যাওয়া হবে, তাই নিয়ে কার্তিক আর গণেশের মারপিট লেগে গেছে। ওই মারপিট থামাতে দুর্গতিনাশিনীকে তাড়াতাড়ি করে টেনে নিয়ে এল মহিষাসুর। বিবাদের কারণ, শুনে মা বলল, তোদের গাড়ি ঠিক করতে কে বলেছে? আমি তো যাব ঘোড়ায় চড়ে। তোর বাবাই ঠিক করে রেখেছেন। যা প্যান্টজামা পরে আয়। এই শুনে সরস্বতীর কী হাসি! কেননা, মারপিট করতে করতে দুই ভাই জামাপ্যান্ট ছিড়ে ফেলেছে। লক্ষ্মী তার স্বভাব গাম্ভীর্য বজায় রেখে জিগ্যেস করল, মা দেবীপক্ষ কি শুরু হয়ে গিয়েছে? দুর্গা বলল, হ্যাঁ। তবে তো ফাইনাল কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গেছে। যাই বাবাকে প্রণাম করে আসি। মহিষাসুর ফুট কাটল, এখন আবার বাবাকে প্রণাম কেন? এন্ড অফ পিতৃপক্ষ। এখন তো মা-ই অল ইন অল।
লক্ষ্মী এই কথায় একটু ক্রুদ্ধ হলেও নিজের নামের মর্যাদা রক্ষায় সচেতন বলে সাইড কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। আর দুর্গা অসুরকে ধমক দিয়ে বলল, কখন কী বলতে হয় শিখলি না! তোকে নিয়ে আমার এই ঝ্যামেলা। জানিস তো লকু বাবার ন্যাওটা। তারপর গলার স্বর নামিয়ে হুকুমের সুরে বলল, যা জোগাড়যন্তর সেরে ফেল। অতএব ফাইনাল হুইসেলের জন্য ঘোড়া কদমতল করা শুরু করল।
হিন্দু শাস্ত্রে মহালয়ার রয়েছে বিশেষ গুরুত্ব ও মাহাত্ব্য। বলা হচ্ছে দেবী দুর্গা স্বয়ং হচ্ছেন সেই মহান আশ্রয়, তাই সেই উত্তরণের লগ্নটির নাম মহালয়া। অন্য একটি অর্থ অনুসারে মহান আলয় হচ্ছে মহালয় বা মহালয়া। আর এই মহা আলয়টি হচ্ছে পিত্রালয় বা পিতৃলোক। জলবিষুব দিবসের পরে আশ্বিন মাসে কৃষ্ণপক্ষের অবসান ও দেবীপক্ষের সূচনায় যে অমাবস্যাকে মহালয়া হিসাবে চিহ্নিত করা হয়, সেই দিনটি হচ্ছে পিতৃপুজো ও মাতৃপজোর সন্ধিলগ্ন। পিতৃপুজো ও মাতৃপুজোর মাধ্যমে এই দিনটিতে হিন্দুরা এই মানবজীবন থেকে পরলোকে পূর্বপুরুষকে জল দেয়, যার শাস্ত্রীয় নাম তর্পণ। এক পুণ্যলগ্ন। ভারতভূমির কোটি কোটি হিন্দু বহু যুগ ধরে মহালয়ার পূণ্য প্রভাতে- ‘ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যান্ত ভুবনত্রয়ম, আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্যন্তং তৃপ্যন্তু’- এই মন্ত্র উচ্চারণ করে তিন গণ্ডুষ জলাঞ্জলি দিয়ে স্মরণ করে চলেছে তাঁদের বিদেহী পিতৃপুরুষ এবং পূর্বপুরুষকে।
পুরাণ মতে, মহালয়ার দিনে, দেবী দুর্গা বরাত পান মহিষাসুর বধের। ব্রহ্মার বর অনুযায়ী কোনও মানুষ বা দেবতা কখনো মহিষাসুর নামে এক মাস্তানকে ঘায়েল করতে পারবে না। আর এই রক্ষাকবচ পেয়েই অসীম ক্ষমতাশালী মহিষাসুর দেবতাদের এনআরসি চালু করল। তালিকা থেকে সব দেবতাদের নাম বাদ দিয়ে স্বর্গে বিদেশি বলে তাড়াতে উদ্যোগী হল। তার লক্ষ্য এক জাতি, এক ভাষা, এক ধর্ম। ঘাবড়ে গেল দেবতারা। ডিটেনশন ক্যাম্পের ভয়ে সবারই আত্মারাম খাঁচা। উপায় খুঁজতে মহিষাসুরের বিরোধীরা জোট করল। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব ত্রয়ী সন্মিলিতভাবে ‘মহামায়া’ রূপে অমোঘ নারীশক্তি সৃষ্টি করল এবং দেবতাদের দশটি অস্ত্রে সুসজ্জিত সিংহবাহিনী দেবী দুর্গা নাকি ন' দিন ধরে যুদ্ধ করে মহিষাসুরকে পরাজিত ও হত্যা করে। তবে যতই পিতৃতর্পণ বা পুণ্যলগ্ন হোক, মহালয়া এলেই বাংলার মাটি-নদী –আকাশ ও পাড়ায় পাড়ায় নানান সংঘ তৈরি হয়ে যায় দশভূজার মহালগ্নকে বরণ করার জন্য। ঢাকের তালে কোমর দোলে, খুশিতে নাচে মন। তবে ১৯৩৬ সাল থেকে বাঙালির কাছে মহালয়া মানে রাত থাকতে ঘুম থেকে উঠে রেডিও খুলে বসা। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের অননুকরণীয় স্বর, আশ্বিনের শারদ প্রাতে বেজে উঠেছে আলোক মঞ্জীর। ঢুলতে ঢুলতে আকাশবাণী 'ক' থেকে 'মহিষাসুরমর্দিনী' শোনা। যদিও ১৯৩২ সালে মহাষষ্ঠীর সকালে প্রথম সম্প্রচারিত হয় ওই অনুষ্ঠান ‘প্রত্যুষ প্রোগ্রাম’ শিরোনামে। পরের বছরও সম্প্রচারিত হল কিন্তু নাম পালটে করা হয় ‘প্রভাতী অনুষ্ঠান’। তার পরের বছরও অনুষ্ঠানটি সম্প্রচার করা হয় তবে মহালয়ার সকালে। এর পর ১৯৩৬ সালে মহালয়ার সকালে সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানটির নাম হয় ‘মহিষাসুর বধ’। তার পরের বছর ফের নাম বদল। হয়ে গেল ‘মহিষাসুরমর্দিনী’। সেই ১৯৩৭ থেকে তা চলে আসছে। মাঝখানে মহানায়ক উত্তমকুমারকে দিয়ে একটা কাউন্টার 'প্রোগ্রাম' চালানো হয়েছিল। কিন্তু বাঙালির ম্যাটিনি আইডল ডাহা ফেল করে গেল। ফিরে এল সেই



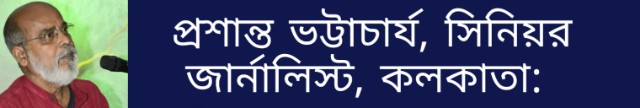

Post A Comment:
0 comments so far,add yours