তপন সান্যাল, কবি, গীতিকার ও গবেষক, পাইকপাড়া, কলকাতা:
তুমি আমার কাছে প্রকাশিত হও তাহলেই । এধি—হে আবিঃ হে প্রকাশ, তুমি তো চিরপ্রকাশ, কিন্তু তুমি একবার আমার হও, প্রকাশ পূর্ণ হোক! হে রুদ্র হে ভয়ানক— তুমি যে পাপের অন্ধকারে বিরোহী রূপে দুঃসহ রুদ্র, স্বত্তে দক্ষিণংমুখং, তোমার যে প্রসন্নস্কন্দয় মুখ, তোমার যে প্রেমের মুখ, তাই আমাকে দেখাও—তেন মাং পাহি নিত্যমৃ—
উপনিষদের এই গভীর কথা যিনি সহজ করে বলে গিয়েছিলেন তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। উপনিষদের এই গভীর উপলব্ধির বীজ তাঁর মধ্যে প্রোথিত হয়েছিল একদম ছোটবেলাতেই। তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন ব্রাহ্ম ধর্মের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সন্তানদের প্রতিদিন, উপনিষদের শ্লোক পড়াতেন, তর্জমা করে দিতেন। বালক রবীন্দ্রনাথের মনে তখন থেকেই এর অনুরণন ঘটতে শুরু করে। ঈশ্বর এবং তাঁর বিশালতার ব্যপ্তি এর অনুভূতির প্রথম বহিঃপ্রকাশ ঘটে যখন তিনি কৈশোরে তাঁর পিতার সঙ্গে হিমালয় ভ্রমণে যান।
রবীন্দ্রনাথের ৮০ বছরের পরিপূর্ণ জীবনের তাঁর মনন, চিন্তন এবং লেখায় আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিভূমি হল ভারতের প্রাচীনতম সনাতন ধর্মের সুপ্রাচীন শাস্ত্র উপনিষদ। তাঁর নিজের কথায় ‘আমার জীবনের মহামন্ত্র পেয়েছি উপনিষদ থেকে’। পরবর্তী কালে যা তার কাব্যগ্রন্থগুলির ছত্রে ছত্রে প্রতিফলিত হয়েছে।
কথায় বলে ‘ব্রাহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণম’ অর্থাৎ যিনি নিজের ক্ষুদ্র সত্ত্বার মধ্যে ব্রহ্মর বিশালত্বকে উপলব্ধি করেন তিনিই ব্রাহ্মণ। ওইখানে ব্রাহ্মণ মানে জাত নয়, বর্ন নয়। এই ব্রহ্মের উপলব্ধি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমস্ত জীবন ব্যাপি জুড়ে ছিল। তিনি সারাজীবন এই ব্রহ্মের অনুসন্ধান করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, উপনিষদের সব পুরুষ ঋষিদের জ্ঞানগম্ভীর বাণীর মধ্যে একটি নারীর ব্যাকুল বাণী ধ্বনিত মন্ত্রিত হয়ে উঠেছে – যা কখনই বিলীন হয়ে যায়নি, তিনি জানতেন অসতো মা সদগময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়। রুদ্র যত্তে দক্ষিণাং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম। অর্থাৎ, হে সত্য, সমস্ত অসত্য হতে আমাকে তোমার মধ্যে নিয়ে যাও, হে প্রকাশ, তুমি একবার আমার হও, আমাতে তোমার প্রকাশ পূর্ন হোক। তাঁর সৃষ্টি, জীবনবোধ এবং সেই অনুযায়ী নিজের জীবনকে গড়ে তোলা সব কিছুতেই ছিল গভীর ঈশ্বরচিন্তা।
প্রথম যে কাব্যগ্রন্থটিতে রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরচিন্তার আভাস পাওয়া যায়, সেটি হল ‘নৈবেদ্য’ কাব্যগ্রন্থ। ধীরে ধীরে তাঁর ঈশ্বর চিন্তার পরিপূর্ন বহিঃপ্রকাশ ঘটে গীতিমালা, গীতালি ও ধর্মসংগীত প্রভৃতি কাব্য এবং গীতিসংকলনে। ব্রহ্মপনিসদ, ব্রহ্মমন্ত্র, উপনিষদ ব্রহ্ম, ভারতবর্ষ, মানুষের ধর্ম, ধর্মের অধিকার প্রভৃতি গদ্যগ্রন্থে বিকশিত হয়েছে তাঁর ঈশ্বরচিন্তা।
তিনি বারবার বলেছেন ‘কোনও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম আমার ধর্ম নয়। আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন, আমি পন্ডিতহারা, আমি তোমাদেরই লোক’। কোনও বিশেষ ধর্ম নয়, শান্তি, মৈত্রী, ব্রহ্মের কাছে নিজেকে বারবার সমর্পিত করতে চেয়েছেন। শুধু কাব্যগ্রন্থই নয় এই আকুলি দেখা গেছে তার গানেও। ’আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধূলার তরে’ গানের এই কথা গুলিতে আত্মসমর্পণের আকুতি ফুটে উঠেছে। শুধু এই গান নয় ব্রহ্মসঙ্গীত, প্রার্থনা সংগীতে বারেবারে তিনি ক্ষুদ্র আমিত্বকে বিশালত্বের কাছে বিলিয়ে দিতে চেয়েছেন। ঠাঁই চেয়েছেন পরম চৈতন্যের কাছে যাহা অসীম। সব কিছুতেই খুঁজতেন, দেখতেন সীমার মাঝে অসীম।
তাঁর সৃষ্টির আধার ছিল উপনিষদ, পরম ব্রহ্ম, সত্যকে উপলব্ধি করা। উপনিষদের শিক্ষাকে তিনি অন্তরের অন্তঃস্থলে সত্যরূপে গ্রহণ করেছিলেন যা তাঁকে করে তুলেছিল ব্রহ্মপাসক। তিনি বলেছেন, ‘উপনিষদ ভারতবর্ষের ব্রহ্ম জ্ঞানের বনস্পতি’। তাঁর এই ব্রহ্ম সাধনার মার্গ তাঁকে করে তুলেছে চিরকালীন। যা দেশ, কাল গন্ডির সীমানা ছাড়িয়ে তাকে দিয়েছে ঋষির মর্যাদা। করে তুলেছে অমরত্বের পথিক।
ব্রহ্ম হলেন "স্থান, কাল ও কার্য-কারণের অতীত এক অখণ্ড সত্ত্বা। তিনি অব্যয়, অনন্ত, চিরমুক্ত, শাশ্বত, অতীন্দ্রিয়।" আত্মা বলতে বোঝায়, জীবের অন্তর্নিহিত অমর সত্ত্বাটিকে। মানে চৈতন্য।উপনিষদের মন্ত্রদ্রষ্টাদের মতে, আত্মা ও ব্রহ্ম এক এবং অভিন্ন। এটিই উপনিষদের সর্বশ্রেষ্ঠ মতবাদ। যেমন কালী অব্যক্ত। এই ব্রহ্মান্ডের বেশির ভাগ অংশই অন্ধকার, এটা বিজ্ঞানীরাও বলছেন, অর্থাৎ কালো যিনি ধারণ করেন উনি কালি। উপাসকরা কালোকে মাতৃরূপ দিয়েছেন মাত্র। তাই মুর্তি এইখানে মাধ্যম, লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য হলো মুক্তি, ব্রহ্ম জ্ঞান, চৈতন্য। এইটি তিনি গভীর ভাবে উপলব্ধি করেছেন, তাই ব্রাহ্ম সমাজে মুর্তি নিষিদ্ধ।
রবীন্দ্রনাথের প্রায় বেশির ভাগ গান হলো ব্রহ্ম সংগীত। যা ধ্রুপদী নিয়মে রচিত। তিনি বিষ্ণুপুর ঘরানা দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। তবে তাঁর উপনিষদ ছাড়াও জীবনে যদি বুদ্ধ না আসতেন, যদি সুফিবাদ ও সন্ত সাহিত্যের কাছে না আসতেন, তিনি রবীন্দ্রনাথ হয়ে উঠতে পারতেন না।
তিনি (ব্রহ্ম) প্রকাশমান বলেই সব কিছু দীপ্তিমান হয়। রবীন্দ্রনাথের দেখায় তা ঠিক এই রকম রূপ নিয়ে নিচ্ছে -
শুধু এই চেয়ে দেখা, এই পথ বেয়ে চলে যাওয়া,
এই আলো, এই হাওয়া,
এইমতো অস্ফুটধ্বনির গুঞ্জরণ,
ভেসে-যাওয়া মেঘ হতে
অকস্মাৎ নদীস্রোতে
ছায়ার নিঃশব্দ সঞ্চরণ,
যে আনন্দ-বেদনায় এ জীবন বারেবারে করেছে উদাস
হৃদয় খুঁজিছে আজি তাহারি প্রকাশ।
[বলাকা – রবীন্দ্ররচনাবলী, ২য় খণ্ড]
যত্র নান্যত্পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স
ভূমাথ যত্রান্যত্পশ্যত্যন্য চ্ছৃণোত্যন্যদ্বিজানা তি
তদল্পং যো বৈ ভূমা তদমৃতমথ যদল্পং তন্মর্ত্যঁ স
ভগবঃ কস্মিন্প্রতিষ্ঠিত ইতি স্বে মহিম্নি যদি বা
ন মহিম্নীতি
[ছান্দোগ্য উপনিষদ]
যার অর্থ – যেখানে মানুষ দেখতে পায় না, কিছু শুনতে পায় না, কিছু উপলব্ধি করে না, তা-ই ভূমা... যা ভূমা তা-ই অমৃত, যা অল্প তা-ই মৃত্যু। সেই ভূমা’র কথাই স্পষ্ট আসছে রবীন্দ্রনাথের বোধে, ঠিক এই ভাবে –
ধূলির আসনে বসি ভূমারে দেখেছি ধ্যানচোখে
আলোকের অতীত আলোকে ।
অণু হতে অণীয়ান মহৎ হইতে মহীয়ান ,
ইন্দ্রিয়ের পারে তার পেয়েছি সন্ধান ।
ক্ষণে ক্ষণে দেখিয়াছি দেহের ভেদিয়া যবনিকা
অনির্বাণ দীপ্তিময়ী শিখা ।
[বর্ষশেষ - পরিশেষ, রবি রচনা ৩য় খণ্ড]
এভাবে দেখতে দেখতে, আনাচে কানাচে লুকিয়ে থাকা ওনার ব্রহ্মজ্ঞানের হীরক খণ্ড এবং রবীন্দ্রসাহিত্যে ব্রাহ্মধর্মের প্রভাব বিস্তারে খুঁজতে গেলে রবীন্দ্রনাথের প্রতিটা পর্বই ছুঁয়ে যেতে হবে। স্বল্প পরিসরে তা সম্ভব নয়। বরং একটা কথা আবার আমাদের মনে করে নেওয়া দরকার যে রবীন্দ্রনাথকে এই ব্রাহ্মধর্মে আবদ্ধ রাখলে এক বিরাট ভ্রান্তির মধ্যে থেকে যেতে হবে। ব্রাহ্মধর্ম, ব্রহ্মজ্ঞান বা উপনিষদ... পরবর্তীকালে বৈষ্ণব পদাবলী, বাউল, সুফি... এসব কিছুর হাত ধরেই রবীন্দ্রনাথের একটাই অন্বেষণ ছিল – রিলিজিয়ন অফ ম্যান। সত্য এবং আনন্দে পরমেশ্বরকে পাওয়া। সেই ‘তোমার মাঝে আমি’ হয়ে থাকার আনন্দই সার।
“I was anxious never to miss a single morning, because each one was precious to me, more precious than gold to the miser. I am certain that I felt a larger meaning of my own self when the barrier vanished between me and what beyond myself.” [The Religion of Man – Rabindranath Tagore]
প্রখ্যাত রবীন্দ্র-জীবনীকার কৃষ্ণ কৃপালনির জবানিতে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, ‘জীবনে একবার মাত্র একটি মুর্তির সামনে আমার প্রণত হওয়ার প্রেরণা জেগেছিল, সেটা বুদ্ধগয়ায়, যখন আমি বুদ্ধমুর্তি দর্শন করি।’ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই উক্তির তাৎপর্য এই যে, ব্যাপারটি তাঁর পরিবার ও সমাজের পক্ষে মোটেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কারণ তাঁরা ব্রাহ্ম, নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক, মুর্তিপূজার ঘোরতর বিরোধী। সেই রবীন্দ্রনাথের হৃদয় ভগবান বুদ্ধ এমনভাবে জয় করেছিলেন যে তাঁর পবিত্র মুর্তির সামনে প্রণাম নিবেদনের জন্য তাঁর অন্তর প্রস্তুত হয়েছিল।
কৃপালনি যে কোনও অতিশয়োক্তি করেননি তার ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত কবি নিজে রেখে গিয়েছেন—কবিতায়, গানে, ভাষণে, ধর্মতত্ত্ব আলোচনায়। ভগবান বুদ্ধদেবকেই কবি ‘অন্তরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলে উপলব্ধি’ করেছেন এবং তাঁর বিচিত্র সৃষ্টির ভিতর দিয়ে তাঁর প্রতি বারবার প্রণাম নিবেদন করে ধন্য হয়েছেন।
১৩৪২ সালে বৈশাখী পূর্ণিমায় কলকাতা মহাবোধি সোসাইটি হলে কবি আমন্ত্রিত ছিলেন। বুদ্ধ-জন্মোৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেদিন যে দীর্ঘ ভাষণটি দেন সেটি বিশ্বসাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদ। তাঁর সেই স্মরণীয় ভাষণ শুরু হয়েছিল এইভাবে—‘আমি যাঁকে অন্তরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলে উপলব্ধি করি আজ এই বৈশাখী পূর্ণিমায় তাঁর জন্মোৎসবে আমার প্রণাম নিবেদন করতে এসেছি। এ কোনও অনুষ্ঠানের উপকরণগত অলংকার নয়, একান্তে নিভৃতে যা তাঁকে বারবার সমর্পণ করেছি সেই অর্ঘ্যই আজ এখানে উৎসর্গ করি।’
কবি কৃতজ্ঞচিত্তে বারবার উচ্চারণ করেছেন, অমেয় প্রেমের মন্ত্র ‘বুদ্ধের শরণ লইলাম’। আমাদের কৌতুহল হয়, রবীন্দ্রনাথের উপর বুদ্ধের এই অপরিমেয় প্রভাব কেন? খোঁজ নিলে দেখা যায় যে, বুদ্ধের জীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথই প্রথম পরিচিত হননি, তাঁর পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সহ তাঁর পরিবারের পরিচয় বরং আরও আগে। বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির বিশিষ্ট স্থান ছিল সিংহল (আজকের শ্রীলঙ্কা)। ১৮৫৯ সালে দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং সিংহল ভ্রমণে যান। সঙ্গী ছিলেন পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ এবং ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম নেতা কেশবচন্দ্র সেন। বঙ্গদেশে মাঝে ক্ষীণ হয়ে আসা বুদ্ধচেতনা নিয়ে তাঁরা ফিরে আসেন। ঠাকুর পরিবারে তা চর্চারও বিষয় হয়ে ওঠে। সত্যেন্দ্রনাথ ‘বৌদ্ধধর্ম’ নামে একটি বই লেখেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ লেখেন ‘আর্যধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত ও সঙ্ঘাত’। সত্যেন্দ্রনাথ বিলেতে গিয়ে প্রখ্যাত ভারতত্ত্ববিদ ম্যাক্স মুলারের সংস্পর্শে পৌঁছে এই বিষয়ে আরও সম্পৃক্ত হয়ে ওঠেন। রবীন্দ্রনাথের উপর তাঁর পিতা ও বহু কৌণিক প্রতিভাধর দাদাদের বিরাট প্রভাবের কথা আমাদের অজানা নয়। অতএব রবীন্দ্রনাথের সমগ্রসত্ত্বা বুদ্ধের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার কারণটি সহজেই অনুমেয়। বুদ্ধের প্রতি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা মিশ্রিত কৌতূহল জাগিয়েছিলেন আর একজন—ইংরেজ কবি এডুউইন আর্নল্ডের ‘লাইট অব এশিয়া’ কাব্যগ্রন্থটি (এটি বুদ্ধের ওপর একটি মহাকাব্য)। এই আর্নল্ড এসেছিলেন ভারতে ২৪ বছর বয়সে। তাঁর এই বইটি যখন প্রকাশিত হয় তখন আর্নল্ডের বয়স ছিল ৪৭, রবীন্দ্রনাথের থেকে অনেক বড়। এই আর্নল্ড রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ ও আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনায় এর প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় যে বুদ্ধগয়াতেও আর্নল্ডের বইটি নিয়ে গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ।
কবি একবার নয়, অন্তত দু’বার বুদ্ধগয়ায় গিয়েছিলেন —১৯০৪ এবং ১৯১৪ সালে। প্রথমবার তাঁর সঙ্গী ছিলেন বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র, ভগিনী নিবেদিতা, ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার- সহ অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি। তাঁরা একত্রে বসে আর্নল্ডের ‘লাইট অব এশিয়া’ এবং হার্ভার্ডের প্রাচ্য বিশারদ হেনরি ক্লার্ক ওয়ারেনের ‘বুদ্ধিজম’ বই থেকে অংশ বিশেষ পড়ে আলোচনা করতেন। শান্তিনিকেতনের শিক্ষক গোঁসাইজিকে উদ্ধৃত করে অধ্যাপক সুধাংশুবিমল বড়ুয়া লিখেছেন, ‘এবার (১৯০৪) বুদ্ধগয়া থেকে আসার পর রবীন্দ্রনাথ মস্তক মুণ্ডন করেছিলেন। তখন কবির মনে নাকি বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়েছিল।’ কবি দ্বিতীয়বার বুদ্ধগয়ায় গিয়ে তিন দিনে দশটি গান লিখেছিলেন—যেগুলিতে ভগবান বুদ্ধের প্রতি অনুরাগ প্রচ্ছন্ন। জাপানযাত্রী কবি ১৯১৬-তে ব্রহ্মদেশের (আজকের মায়ানমার) তৎকালীন রাজধানী রেঙ্গুনে (আজকের ইয়াঙ্গন) পা রাখেন। পরদিন ছিল ২৫ বৈশাখ। জন্মদিনের সকালে কবি সেখানকার বিখ্যাত শোয়েডেগান বৌদ্ধমন্দির দর্শন করে অভিভূত হন। ওই মন্দিরের ভিতরেই তিনি বিরাট ব্রহ্মদেশের নিজস্বতার প্রকাশ আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল, কোনও এককালে ভারতীয় সাধনার আলোকে ব্রহ্মদেশের হৃদপদ্ম বিকশিত হয়েছিল। ওই মন্দিরের ভিতরে কবি উপলব্ধি করেছিলেন তারই প্রকাশ। সেদিন তাঁর মনে এমন ভাবের উদয় হয়েছিল যে, শুধুমাত্র ব্রহ্মদেশের অচেনা কোনও এক গাঁয়ের বৌদ্ধমঠে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকতে পারলে বেশ আরাম পাবেন ভেবেছিলেন। কবি চীনে যাওয়ার পথে ১৯২৪-এও ফের রেঙ্গুনে অবস্থান করেন। নাগরিক সংবর্ধনার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ ‘মৈত্রীর আদর্শ’কেই ভারতের শ্রেষ্ঠ দান বলে উল্লেখ করেন। এর ভিতরে তিনি যে বুদ্ধের নীতিকেই ইঙ্গিত করেছিলেন তা বুঝতে বাকি থাকে না। বৌদ্ধ সংস্কৃতির টানে কবি তিনবার সিংহলে এবং দ্বীপময় ভারতে (থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, জাভা, সুমাত্রা, বালি প্রভৃতি) গিয়েছেন।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের হিংসার নীতি কবিকে ভীষণ ব্যথিত করে। আক্রান্ত চীনের জন্য কবির মন কেঁদে উঠেছিল। দুই সুপ্রাচীন সভ্য দেশের ধর্ম ও সংস্কৃতির নিবিড় আত্মীয়তাকে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। চীনবাসীদের জন্য প্রাণভরা ভালোবাসা শুভেচ্ছা নিয়ে কবি চীনে পাড়ি দেন ১৯২৪-এ। কবি সেদিন নানা ভাবে চীনের জয় কামনা করেছিলেন। তিনি আশা ব্যক্ত করেছিলেন, অতীতের সাধনা যেমন ভারত ও চীনকে মৈত্রীর বাঁধনে বেঁধেছিল অদূর ভবিষ্যতেও সেই শক্তি দুই প্রতিবেশীকে প্রীতির বাঁধনে বাঁধবে। হাংচৌ, সাংহাই, পিকিং, নানকিং প্রভৃতি শহরে কবির জন্য অনেকগুলি সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। পিকিঙে অবস্থানকালে নির্বাসিত মাঞ্চু সম্রাট কবিকে তাঁর প্রাসাদে সাদর অভ্যর্থনা জানান। কবির হাতে উপহার হিসেবে সম্রাট তুলে দেন অমূল্য এক বুদ্ধমূর্তি— চীনের ইতিহাসে এক বিরল সম্মান প্রদর্শন। কবির চীন সফরকালে পড়ল ২৫ বৈশাখ, কবির জন্মদিন। ক্রিসেন্ট মুন সোসাইটি বিশেষ চৈনিক রীতিতে সেদিন তাঁর সম্মানে এক উৎসবের আয়োজন করে। বিশিষ্টজনেরা তাঁকে ভারত-চীন ঐক্যের প্রতীক হিসেবে উল্লেখসহ ‘চু-চেন-তান’ উপাধি প্রদান করেন।
বৌদ্ধ কালচারের প্রতি কবির অনুরাগ এতটাই গভীর ছিল যে, পৃথিবীর নানা প্রান্তের বৌদ্ধ পণ্ডিতদের শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতীতে সামিল করেছিলেন। যেমন ফ্রান্সের সিলভ্যাঁ লেভি, চীনের লিন ও-চিয়াং এবং রোমের জোসেপ তুচ্চি। লেভিই বিশ্বভারতীর প্রথম অতিথি অধ্যাপক। আচার্য লেভিরই আন্তরিকতায় বিশ্বভারতীতে চীনভবন প্রতিষ্ঠা-সহ বৌদ্ধশাস্ত্র গবেষণার ব্যবস্থা হয়। বলা বাহুল্য, ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিতও ছিলেন একাধিক।
এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করার মতো একটি তথ্য এই যে, কলকাতায় মহাবোধি সোসাইটি প্রতিষ্ঠার দু’বছর বাদে ১৮৯৩-তে শিকাগো বিশ্ব ধর্মমহাসভায় বৌদ্ধধর্মের প্রতিনিধিত্ব করেন সিংহলের তরুণ অনাগারিক ধর্মপাল। সেখানেই স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের এই দুই তরুণ নেতার প্রীতির সম্পর্কের বিষয়টি কবিরও দৃষ্টি এড়ায়নি। ধর্মপাল কলকাতায় ফিরে বুদ্ধচেতনায় ভারতবাসীকে জাগাতে চেষ্টা করেন। বৈশাখী পূর্ণিমায় বুদ্ধ-জয়ন্তী পালনেরও উদ্যোগ নেন তিনি। বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ লেখেন তাঁর বিখ্যাত দু’টি গান—‘হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী’ এবং ‘সকল কলুষ-তামস হর’।
শুধু ধর্ম নয় রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্র ও সমাজচিন্তার ভিতরেও বুদ্ধের আদর্শের গভীর প্রভাব ছিল। বুদ্ধকে উদ্ধৃত করে কবি আমাদের সাবধান করে গিয়েছেন, বাহুবলের সাহায্যে ক্রোধ -প্রতিহিংসাকে জয়ী করে শান্তি মিলবে না। শান্তির উপায় হচ্ছে ক্ষমা। রাষ্ট্র ও সমাজনীতিতে এই জিনিস মানুষ যতদিন না স্বীকার করবে ততদিন অপরাধ বেড়ে চলবে। রাষ্ট্রগত বিরোধের আগুন নিভবে না। পৃথিবীর মর্মান্তিক পীড়া উত্তরোত্তর দুঃসহ হতে থাকবে। কোথাও এর শেষ পাওয়া যাবে না।
যুদ্ধক্লান্ত তৎকালীন ইউরোপ রবীন্দ্রনাথকে মানবপ্রেমিক আবিষ্কার করেছিল। কিন্তু সে ছিল রাজনীতির ক্ষেত্রে। পশ্চিমের মানুষ জানত না যে সাহিত্যক্ষেত্রেও তিনি সর্বাগ্রে মানবপ্রেমিক। আরও বিশদে বলা যায় যে তাঁর সমস্ত প্রেম ছিল জীবন ও মাটির পৃথিবীটার জন্য। স্বর্গের চাইতে মর্ত্যকে, পরলোকের চাইতে ইহলোককে এবং দেবতার চাইতে মানুষকেই বেশি মূল্য দিয়েছেন তিনি। যেখানে বিবেকানন্দ বুদ্ধকে ভগবান বুদ্ধ বলছেন রবীন্দ্রনাথ বলছেন না উনি শ্রেষ্ঠ মহামানব। এরপর বুঝতে অসুবিধা হয় না, সবাই যাঁকে ‘ভগবান’ বুদ্ধ বলেছেন, কবি কেন তাঁকে প্রণাম নিবেদন করতে গিয়ে অন্তরের সমস্ত শ্রদ্ধা ঢেলে ‘শ্রেষ্ঠ মানব’ বলে উল্লেখ করেছেন। এইখানে উল্লেখ করা দরকার বেদান্তে ভগবান সম্পর্কে কি উল্লেখ করা হয়েছে যেটা রবীন্দ্রনাথ খুব ভালো ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। এই দেশে ঈশ্বর বলতে কোনও অলৌকিক ক্ষমতাকে বোঝায় না। এইখানে এই দেশে মানুষই ভগবান যেটা খুব অল্প মানুষ অনুধাবন করতে পারেন।
যার রূপ থাকে, তাকে যেমন বলে রূপবান; তেমনি- যশ, বীর্য, ঐশ্বর্য, শ্রী, জ্ঞান, বৈরাগ্য- এই ছয়টি গুনকে বলে ‘ভগ’ আর এগুলো যার মধ্যে থাকে, তাকে বলে ভগবান; আর সকল গুন যার মধ্যে থাকে তাকে বলে ঈশ্বর। অন্য ভাষায় ঋষি অরবিন্দ বলেছেন, Divine alone is god। উপনিষদে ঈশ্বর কোনও অপার্থিব বস্তু নয়। মানুষই শেষ কথা। Let unknown god bless them। কি মানে এর? Unknown god। একজন প্রশ্ন করেছে, এতো করোনায় মানুষ মরছে ভগবান কি আদৌ আছে।? What is unknown god? God is not known to us. It's a belief only। আর যখনই এটা বিশ্বাস তার মানেই সন্দেহ আছে। if u have mastery over your mind, means u can fully control your mind। তুমি দুঃখেও ভেঙে পড়ছো না আবার সুখেও উত্তেজিত নও, কিন্তু cool আছো। Then u r a god। If can't feel or unable to see that u r connected with great cosmos then god is unknown to u।
আমাদের সবার ভিতরেই আছে চৈতন্য। কিন্তু মানুষ ছুঁতে পারে না। যে ছুঁতে পারে সেই তো ঈশ্বর। আর উপরওয়ালা বলে কিছু নেই, নিচওয়ালা কথাটা অনেক জীবন্ত এবং বাস্তবিক। যেটাকে রবীন্দ্রনাথ ইহলোক বলছেন। আমাদের দেশে ভগবান বলতে কোনও অলৌকিক শক্তিকে বোঝায় না। মানুষই ভগবান কিন্তু খুব কম মানুষ এটা অনুভব করতে পারে বা বুঝতে পারে।
গৌতম বুদ্ধের একটা গল্প আছে। এইটা বলা এইখানে প্রাসঙ্গিক। একদিন সকালে এক চার্বাক পন্থী জিজ্ঞেস করলো বুদ্ধকে ঈশ্বর কি আছেন? বুদ্ধ খুব কম কথা বলতেন, উনি বুঝেছিলেন যে এই ব্যক্তি ঈশ্বর বিরোধী। বুদ্ধ উত্তরে বললেন ' ঈশ্বর আছে।' এইবার ওই দিন বিকেলে আর একজন ঈশ্বর বিশ্বাসী মানুষ এলেন। উনি বুঝলেন বুদ্ধ হলো আত্ম জ্ঞানী মানুষ উনাকে জিজ্ঞেস করা যাক। জিজ্ঞেস করলেন ঈশ্বর কি আছে? বুদ্ধ হেসে বললেন' ঈশ্বর নেই।' সবাই অবাক হয়ে গেল কেন বুদ্ধ একই দিনে দুই রকম কথা বললেন। আসলে বুদ্ধ বোঝাতে চেয়েছিলেন তোমরা অনুসন্ধান করো কেবল বিশ্বাসে থেমে থেকো না। অর্থাৎ যে মানুষটি বিশ্বাস করে ভগবান নেই আর যে বিশ্বাস করে ভগবান আছে এরা সবাই একই জায়গায় আছে। প্রত্যেকেরই সন্দেহ আছে তাই বিশ্বাস ও অবিশ্বাস এর মধ্যে আছে। ঈশ্বর আছে কিন্তু তোমরা যে ভাবে ঈশ্বরকে দেখতে চাইছো ওই ভাবে কোনও ঈশ্বর নেই। it's better to doubt than to belief।
ভিন্ন ভিন্ন পথে খুঁজে নাও সত্য কি? কোনও একটি পথ সত্য নয়। যত মত তত পথ। ওই কারণেই god is unknown। রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন বিবেকানন্দের মতো মানব সেবা শ্রেষ্ঠ ধর্ম। ওই কারণেই কবি চন্ডী দাসকে শুধু গুরুত্ব দিয়েছেন শুধু তাই নয় বলেছেন তিনি মনুষ্যত্বের কবি, দুঃখের কবি। কবি চন্ডী দাস বলেছিলেন সবার ওপরে মানুষ বড় তাঁহার ওপরে নেই। রবীন্দ্রনাথ বললেন সবার ওপরে মানুষ সত্য তাঁহার ওপরে কেউ নাই। এটাই সংস্কৃতির বিবর্তন এবং উপনিষদের মর্ম বানীর প্রয়োগ। তাই তো তিনি তাঁর বুদ্ধ প্রবন্ধে বললেন, আলেকজান্ডার পৃথিবী জয় করেননি। পৃথিবী জয় করেছেন গৌতম বুদ্ধ।
রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হলেও তাঁর আধ্যাত্মিকতার উপলব্ধি সেই গণ্ডির বাইরে ছিল। ১৩১৫ সালে শান্তিনিকেতনে মাঘোৎসবের ভাষণে তিনি ‘ব্রাহ্মোৎসব’কে ‘ব্রহ্মোৎসব’ আখ্যা দান করেন। কোনও সম্প্রদায়ের উৎসব না হয়ে মানবসমাজের উৎসব হয়ে ওঠে তা। বিশেষ ধর্মের মধ্যে সীমায়িত ছিল না তাঁর আধ্যাত্মিকতা। ধর্মসমন্বয় ও জাতিসমন্বয়ের কথাই বারবার উচ্চারিত হয়েছে তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে।
শান্তিনিকেতনের মন্দিরে কবি যিশু খ্রীস্ট, চৈতন্য সম্পর্কে ভাষণ দিয়েছিলেন। গৌতম বুদ্ধ ও হজরত মুহম্মদের (সা.) স্মরণদিন পালন করা শুরু করেছিলেন। ধর্ম সম্পর্কে কবির উপনিষদের জ্ঞান পূর্ণতা পায় মধ্যযুগীয় সাধু-সন্তদের জীবনীর আলোকে। ভারতের ধর্মসাধনার ধারা বহন করেছেন তিনি। রবীন্দ্রজীবনী রচয়িতা প্রভাতকুমার বলেছেন, ‘তাঁর ধর্ম মানবতার ধর্ম-কর্মে কঠোর, জ্ঞানে উজ্জ্বল, ভক্তিতে রসাপ্লুত, সৌন্দর্যে সমন্বিত।’(পৃ. ২৬৭) প্রবোধচন্দ্র সেন রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা সম্পর্কে বলেছেন, ‘রবীন্দ্রনাথ সেই ধর্মকেই চেয়েছিলেন যাতে জ্ঞান প্রেম ও কর্ম মিলিত হয়েছে, যাতে উপনিষদের সত্যসাধনা, বৌদ্ধধর্মের মৈত্রী-করুণা এবং বৈষ্ণব ও খ্রীস্টধর্মের প্রেমভক্তি একত্র সমন্বিত হয়েছে, অথচ যা সর্বতোভাবেই আধুনিক শিক্ষিত মনের উপযোগী। সে মন একান্তভাবেই সাম্প্রদায়িক ভেদবিভেদ, আচারপদ্ধতি ও আনুষ্ঠানিকতার বিরোধী।’
শুধু বিশ্ব জনীন আলোকপ্রাপ্ত দৃষ্টি যথেষ্ঠ নয়। যেটা বই পড়ে ও হয় না শোক ও মৃত্যুর গভীর বোধ তাঁর জীবনে নেমে এসেছিল। অর্থাৎ তিনি রবীন্দ্রনাথ হয়ে উঠছেন। তবু একবার চেয়েছিলেন অপঘাতে প্রাণ যাক! কিন্তু কেন?
মারা যেতে পারতেন অকালে। এক সময় ভেবেছিলেন ‘শেষ’ করে দেবেন নিজেকে! কবির জীবনে মরণের যে কী নিরবচ্ছিন্ন বিধ্বংসী খেলা! ডুবেই যেতেন নদীতে। পূর্ববঙ্গের পান্টি থেকে বোটের পাল তুলে আসছিলেন। গোরাই ব্রিজের নীচে এসে বোটের মাস্তুল আটকে গেল ব্রিজে। এক দিকে নদীর স্রোত প্রবল ধাক্কা মারছে নৌকাকে, অন্য দিকে ব্রিজে-আটকানো মাস্তুল টেনে ধরে রেখেছে তাকে। মড়মড় করে মাস্তুল যখন হেলতে শুরু করেছে, কোত্থেকে একটা খেয়া নৌকো এসে উদ্ধার করে রবীন্দ্রনাথকে! বোটের কাছি নিয়ে দু’জন মাল্লা জলে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতরে ডাঙায় উঠে টেনে আনল খেয়া। ২০ জুলাই, ১৮৯২। শিলাইদহ থেকে স্ত্রী মৃণালিনীকে রবীন্দ্রনাথ সেই দুর্ঘটনার কথা জানিয়ে লিখলেন, ‘‘ভাগ্যি সেই নৌকো এবং ডাঙ্গায় অনেক লোক উপস্থিত ছিল, তাই আমরা উদ্ধার পেলুম, নইলে আমাদের বাঁচার কোন উপায় ছিল না।’’ আর লিখলেন, ‘‘মাঝিরা বলছে এবার অযাত্রা হয়েছে।’’ গনতকার রায় দিয়েছিলেন অকালমৃত্যুর।
১৮৯২-এর জুন। জমিদারি দেখাশোনার কাজে পরিবার থেকে দূরে সেই পূর্ববঙ্গে সাহাজাদপুরে রবীন্দ্রনাথ। স্ত্রী মৃণালিনীকে মাঝে মাঝেই চিঠি লেখেন। উত্তর না পেলে অভিমান করেন। একদিন লিখেছিলেন এক গনতকারের কথা। এলাকার প্রধান গনতকার। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, নিজের জীবনে কবি মোটে সঞ্চয়ী হবেন না, তাঁর স্ত্রী-টি বেশ ভালো, যাঁদের উপকার করেছেন তাঁরাই তাঁর অপকার করবে। আর শেষে মোক্ষম ভবিষ্যদ্বাণী— কবির আয়ু বড়জোর ষাট অথবা বাষট্টি বছর। কোনও মতে সে-বয়স কাটিয়ে দিতে পারলেও জীবন নাকি কিছুতেই পেরোবে না সত্তরের গণ্ডি। তাতে চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। মৃণালিনীকে লিখেছিলেন, ‘‘শুনে তো আমার ভারী ভাবনা ধরিয়ে দিয়েছে। এই তো সব ব্যাপার। যা হোক তুমি তাই নিয়ে যেন বেশি ভেবো না। এখনো কিছু না হোক, ত্রিশ চল্লিশ বছর আমার সংসর্গ পেতে পারবে।’’ এই চিঠি লেখার এগারো বছরের মাথায় নভেম্বর মাসের একদিন। কী আশ্চর্য! চলে গেলেন মৃণালিনী! মৃত্যু কত অনিশ্চিত। শোকে পাথর রবীন্দ্রনাথ। দর্শনার্থীদের ভিড় ফিকে হয়ে গেলে মৃণালিনীর সব সময় ব্যবহারের চটিজুতো- জোড়া তুলে দিলেন রথীন্দ্রনাথের হাতে। বললেন, ‘‘এটা তোর কাছে রেখে দিস, তোকে দিলুম।’’
আর বাইশ বছর পর, ২ নভেম্বর ১৯২৪। মৃণালিনীকে স্মরণ করে আন্দেজ জাহাজে বসে লিখলেন, "...তোমার আঁখির আলো, তোমার পরশ নাহি আর,/ কিন্তু কী পরশমণি রেখে গেছ অন্তরে আমার—/ ...সঙ্গীহীন এ জীবন শূন্যঘরে হয়েছে শ্রীহীন,/ সব মানি— সবচেয়ে মানি, তুমি ছিলে একদিন।’’
শোকের দহন যেন তখনও তাঁর ভিতরে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছাড়াও, এই দর্শনে দীক্ষিত হয়েই জীবন আর মৃত্যু নিয়ে তাঁর নিজের একটা ধারণা গড়ে উঠেছিল। জীবনের মধ্যে থেকে মৃত্যুকে আর দুঃখকে সহজে বরণ করার কথা তিনি বারবার বলেছেন।
উপনিষদ থেকে তাঁর ভাবানুবাদ করা এই শ্লোক যেন তাঁর নিজের মৃত্যু চিন্তারই প্রতিধ্বনি: ‘‘শোনো বিশ্বজন, শোনো অমৃতের পুত্র যত দেবগণ/ দিব্যধামবাসী। আমি জেনেছি তাঁহারে মহান্ত পুরুষ যিনি/ আঁধারের পারে জ্যোতির্ময়।/ তাঁরে জেনে তাঁর পানে চাহি/ মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পার, অন্য পথ নাহি।’’
না হলে কি করে লিখলেন?
মরণ রে, তুঁহু মম শ্যামসমান।
জীবন ও মৃত্যুর মাঝামাঝি যে শান্ত শোক নদী বয়ে চলে যায় ( জীবন ও মৃত্যুর চক্রের নদী যা অনন্ত)। আমরা তাকে অশান্ত রূপে দেখি। কারণ অনন্ত রস ও রূপের সাথে আমরা যুক্ত হতে সমর্থ নই। জীবন যখন অপ্রকট হয়ে যায় সেটাই মৃত্যু। আবার সময় এলে জীবন জাগে। ঠিক গাছের মতো ব্যক্তিগত ভাবে মৃত্যু আছে কিন্তু সার্বজনীন ভাবে দেখলে নেই। জীবন ও ফুল ও ফলের মতো সময় হলে আবার ফোটে। তাই মৃত্যু নেই চতুর্দিকে জীবনই জীবন। কবিগুরু সঠিক বলেছেন,
আছে দুঃখ আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে।
তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে॥
তবু প্রাণ নিত্যধারা, হাসে সূর্য চন্দ্র তারা,
বসন্ত নিকুঞ্জে আসে বিচিত্র রাগে॥
তরঙ্গ মিলায়ে যায় তরঙ্গ উঠে,
কুসুম ঝরিয়া পড়ে কুসুম ফুটে।
নাহি ক্ষয়, নাহি শেষ, নাহি নাহি দৈন্যলেশ--
সেই পূর্ণতার পায়ে মন স্থান মাগে॥
প্রায় ৬৫ বছর ধরে তিনি স্বজনের মৃত্যু দেখেছেন।
তাই তিনি মরণ বিজয়ী রবীন্দ্রনাথ।
স্বজনহারা রবি
১৮৭৫ সারদাসুন্দরী দেবী, মা
১৮৮১ গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভ্রাতুষ্পুত্র
১৮৮৩ সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, জামাইবাবু, রবীন্দ্রনাথের বিয়ের রাতে মারা যান
১৮৮৪ হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সেজদাদা
১৮৮৪ কাদম্বরী দেবী, বৌদি, আফিম খেয়ে আত্মহত্যা করেন
১৮৯৪ বিহারীলাল চক্রবর্তী, আদর্শ কবি, মৃত্যুর পরে রবীন্দ্রনাথের বেয়াই
১৮৯৫ অভিজ্ঞা চট্টোপাধ্যায়, ভ্রাতুষ্পুত্রী
১৮৯৭ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ভগ্নিপতি, ক্যানসারে মৃত্যু
১৮৯৯ উষাবতী চট্টোপাধ্যায়, ভ্রাতুষ্পুত্রী
১৮৯৯ বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভ্রাতুষ্পুত্র, যক্ষ্মায় মৃত
১৯০১ নীতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভ্রাতুষ্পুত্র
১৯০২ মৃণালিনী দেবী, স্ত্রী, মারা যাবার সময় বয়েস ঊনত্রিশ
১৯০৩ বিমানেন্দ্রনাথ রায়, বাবার শ্যালকের ছেলে
১৯০৩ দ্বিতীয় কন্যা রেণুকা ভট্টাচার্য, যক্ষ্মায় মৃত
১৯০৫ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাবা
১৯০৭ শমীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কনিষ্ঠ পুত্র, কলেরায় মৃত
১৯০৮ সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, জামাতা, দ্বিতীয় কন্যা রেণুকার স্বামী
১৯০৮ হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভ্রাতুষ্পুত্র
১৯১০ নীপময়ী ঠাকুর, বৌদি, স্ত্রী মৃণালিনীর শিক্ষিকা
১৯১৩ জানকীনাথ ঘোষাল, ভগ্নিপতি, ‘ভারতী’-র সম্পাদক
১৯১৫ বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দাদা
১৯১৬ শান্তা বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাগ্নের মেয়ে
১৯১৮ ইরাবতী মুখোপাধ্যায়, ভাগ্নি, বাল্যসখী
১৯১৮ মাধুরীলতা চক্রবর্তী, জ্যেষ্ঠ কন্যা, যক্ষ্মায় মৃত
১৯১৯ জ্যোতিঃপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, দাদার মেয়ের ছেলে, শৈশবে কবিতার দীক্ষাদাতা
১৯১৯ সুকেশী ঠাকুর, ভ্রাতুস্পুত্রের স্ত্রী
১৯২০ শরৎকুমারী মুখোপাধ্যায়, দিদি
১৯২০ সৌদামিনী গঙ্গোপাধ্যায়, দিদি
১৯২২ তিভাসুন্দরী চৌধুরী, ভাগ্নি
১৯২২ সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দাদা
১৯২৩ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দাদা
১৯২৪ আশুতোষ চৌধুরী, বন্ধু, ভাগ্নির স্বামী
১৯২৪ বিনয়িনী চট্টোপাধ্যায়, বেয়াই, পুত্র রথীন্দ্রের শাশুড়ি
১৯২৫ হিরণ্ময়ী মুখোপাধ্যায়, ভ্রাতুষ্পুত্রী
১৯২৫ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘নতুন দাদা’
১৯২৬ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বড় দাদা
১৯২৯ অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভ্রাতুষ্পুত্র
১৯২৯ মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, অবনীন্দ্রনাথের জামাতা, কবির প্রিয়পাত্র
১৯২৯ সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভ্রাতুষ্পুত্র
১৯৩২ নীতীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, দৌহিত্র
১৯৩২ স্বর্ণকুমারী দেবী, দিদি
১৯৩৩ সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, ভাগ্নে
১৯৩৫ কৃতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভ্রাতুষ্পুত্র
১৯৩৫ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভ্রাতুষ্পুত্র
১৯৩৭ ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভ্রাতুষ্পুত্র
১৯৩৮ গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাকার ছেলে
১৯৪০ সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভ্রাতুষ্পুত্র
(www.theoffnews.com - Rabindranath Tagore Goutam Buddha)

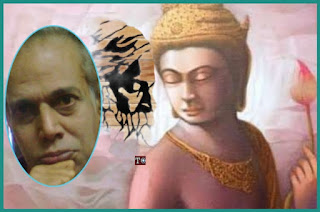



Post A Comment:
0 comments so far,add yours